
রিডিং ক্লাব ট্রাস্টের ৪৫০তম সাপ্তাহিক লেকচার
বক্তা: ড.আদনান জিল্লুর মোরশেদ
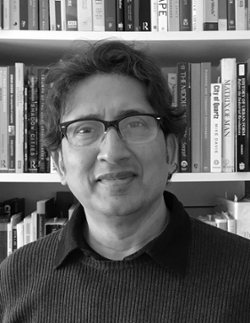
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থাপত্যের দৃষ্টিতে দেখতে হলে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে দেখতে হবে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদের প্রেক্ষাপটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার কারণে মানুষের মনে এমন চিন্তা রয়েছে যে ঔপনিবেশিক ভেদনীতির ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গভঙ্গ রদের পর ঢাকায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু হলেও এতে সাম্প্রদায়িকতার ছোয়া লাগেনি। ভাইসরয় লিটনের বরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের সুন্দর উপহার। তবে এসবের বাইরে গিয়ে নিজস্ব আঙ্গিকে দেখলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনব যাত্রা উপলব্ধি করা যাবে। এরকম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের এখানকার পরিপ্রেক্ষিতে এতে নতুনত্ব ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র পশ্চাতধর্মী মুসলমানদের শিক্ষিত করার জন্য তৈরি হয়নি। বরং হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য ১৯২১ সালে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখা হয়েছিল আন্তর্জাতিক মানের মননশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। দেখা হয়েছিল বৈশ্বিক মানবতাবাদী প্রতিষ্ঠান হিসেবে। নাথান কমিশনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, এখানে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে গিয়ে কাজ করা হয়েছে। ফিলিপ হার্টগের বিভিন্ন লেখায়ও তা স্পষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ফিলিপ হার্টগ ছিলেন একজন ইহুদী।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য পি.জে হার্টগ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। ১৭ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার ছিলেন। তিনি সারা পৃথিবী থেকে অনেক জ্ঞানী-গুণী মানুষের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। যদি শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক ভেদনীতির আলোকে দেখি, তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক যাত্রায় বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারবো না। বৈশ্বিক জ্ঞানার্জনের কার্যক্রম নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ঢাকা বিশ এবং ত্রিশের দশকে এখানে সংঘটিত হয়েছিল ‘বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন’। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞান উৎপাদনের জন্য দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হতে দেখা গিয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ তৈরি করার বাতিঘর হিসেবে দেখা যেতে পারে। এখানে স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারকে ঘিরে একটি সার্বজনীন শিক্ষা কার্যক্রম গড়ে উঠেছিল। সেই ধারাবাহিকতায় একে স্থাপত্য ও নগরচর্চার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে এর ধারণা ও ব্যাপ্তি আরো প্রসারিত হবে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল বুড়িগঙ্গা থেকে উত্তরে ঢাকা শহরের সম্প্রসারণ দিকে। এই সম্প্রসারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩০০ একরের বেশি জমি দেওয়া হয়েছিল। রমনা পার্ক এবং রেসকোর্সের (বতর্মানে সোওরাওয়ার্দী উদ্যান) মধ্যে একটা প্রাকৃতিক পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয়টি নির্মাণ করা হয়েছিল। অল্প কয়েকটি ভবন নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। এর আগে ঢাকায় নতুন প্রদেশের রাজধানী স্থাপনের লক্ষ্যে কিছু স্থাপত্য-তৎপরতা দেখা যায়। যেমন, ১৯০৪ সালে কার্জন হল স্থাপন করা হয়েছিল। কারো কারো মতে, কার্জন হলকে ঢাকা শহরের সিটি হল হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ঢাকা শহর ছিল একটা বড় গ্রামের মতো। তবে সেই সময়ে ঔপনিবেশিক কিছু নগর তৎপরতা দেখা গিয়েছিল। সেখানে কার্জন হল, গভর্নর হাউজ স্থাপন করা হয়। ঢাকা শহরের রক্ষার জন্য বুড়িগঙ্গায় বাকল্যান্ড বাঁধ নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া নগর প্রশাসনের কিছু দপ্তর নির্মাণ করা হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় উপাচার্য ল্যাংলি সার্বজনীন শিক্ষা কার্যক্রমকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ২০ এর দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজের কেন্দ্রবিন্দু। ৫০ এর দশকে দেশভাগের পরেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশ্বিক শিক্ষা কার্যক্রমের কোনো পরিবর্তন হয়নি। দেশভাগের ১০ বছর পরে ১৯৫৭ সালে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ চালু করা হয়। এবং এর পিছনে ভূমিকা রাখেন ক্লড লেভি স্ট্রস। তিনি বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় নৃতাত্ত্বিক গবেষণার কাজে এসেছিলেন। তার অনুপ্রেরণায় সমাজবিজ্ঞান বিভাগের যাত্রা শুরু।
১৯৫০ এর দশকে পূর্ববঙ্গের নান্দনিক স্থাপত্যের সূত্রপাত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত ধরেই। স্থপতি মাজহারুল ইসলাম কলকাতায় পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি চারুকলা ভবনের নকশা করেন। ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের নকশাও তার করা। চারুকলা অনুষদকে বাংলাদেশের স্থাপত্যে নান্দনিক আধুনিকতার সূত্রপাত বলা যেতে পারে। কারণ,চারুকলা অনুষদটি কার্জন হল দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়। এর নকশা ভিন্ন, ইন্দো ইউরোপীয় বা ইন্দো সারাসেনিক ধারা থেকে আলাদা। এছাড়া এটি অলঙ্কারবিহীন, প্রকৃতির প্রতি স্পর্শকাতর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতেও এরূপ দেখা যায়। অর্থাৎ ইন্দো সারাসেনিক প্রভাব মুক্ত।এটার আধুনিক স্থাপত্য ধারাকে সামাজিক সাংস্কৃতিক বিশুদ্ধকরণ বলা যেতে পারে।
২০ এর দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সার্বজনীন শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় ৫০ এর দশকে নান্দনিক স্থাপত্যের আধুনিক ধারার যাত্রা শুরু। এসময়ে শিক্ষা কার্যক্রম ও রাজনীতিকরনের প্রভাব দেখা যায়। স্থাপত্যের আধুনিক ধারার আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে টিএসসি। টিএসসির স্থপতি ছিলেন একজন গ্রীক স্থাপত্যপরিকল্পনাবিদ। টিএসসির ক্ষেত্রে নতুন ধারার স্থাপত্যশৈলী অনুসরণ করা হয় যা গ্রীষ্মমন্ডলীয় পরিবেশের জন্য অনুকূল।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নগর পরিকল্পনার অগ্রযাত্রার পাশাপাশি পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রেক্ষাপটেও দেখা যেতে পারে। বিখ্যাত স্থপতিগণ তাদের পরিবেশভিত্তিক ধ্যান ধারনা দ্বারা একে আরো উন্নত করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান উৎপাদনের পাশাপাশি স্থাপত্য চর্চায়ও দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হয়েছিল।