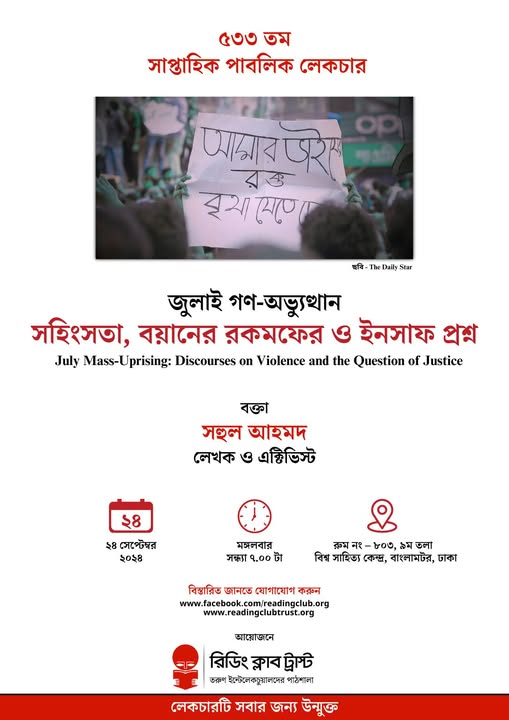
জুলাই মাসের মাঝামাঝি কোটা সংস্কার আন্দোলন যে পর্যায়ে পৌঁছানো, তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পতনের মাধ্যমে। বিগত দেড় দশকের আওয়ামী রেজিমকে ফ্যাসিবাদী, উর্দিবিহীন স্বৈরতন্ত্র, নিখোঁজ গণতন্ত্র, কর্তৃত্ববাদী ইত্যাদি নানা বর্গে চিহ্নিত করলেও এর কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রায় সকল বর্গতেই হাজির ছিল। টানা তিন মেয়াদে কারচুপির নির্বাচন, পদ্ধতিগত গুম, খুন, ক্রসফায়ার (বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড), মতপ্রকাশে দমনপীড়ন ও অর্থ-পাচার ছিল গণতন্ত্রহীন হালতে উপনীত হওয়ার নির্ধারক। ফলে, চাকরিজনিত ইস্যুর উছিলায় মূল আন্দোলন মাঠে গড়ালেও সরকারি দমনপীড়ন এবং গত এক দশকের বেশি সময় ধরে অগণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার অধীনে বসবাসের যন্ত্রণা পুরো জনগোষ্ঠীকে বিদ্যমান রাষ্ট্র ও ক্ষমতাকাঠামো পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রবল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার দিকে ধাবিত করে।
নব্বইয়ের গণআন্দোলনের অভিজ্ঞতা, উর্দিপরা থেকে উর্দিহীন হালতে আবারও স্বৈরতন্ত্রের আবির্ভাব এবং সংবিধানকে ব্যবহার করে আওয়ামী রেজিমের ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের গণপরিসরে (পাবলিক স্ফেয়ার) রাষ্ট্রের সংস্কারকে বা আশু কর্মসূচি হিসাবে হাজির করেছিল। গত ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে নীরবতা ও স্থবিরতা নেমে এসেছিল, শিক্ষার্থীদের তৎপরতা সেটাকে কেবল উড়িয়েই দেয়নি, বরঞ্চ দ্রুততার সহিত শাসকের পতনও ঘটিয়ে দিয়েছে। যদিও, মনে হতে পারে, এটা দ্রুততার সাথে ঘটেছে, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যে রেজিম যত দীর্ঘমেয়াদী, তার পতনও তত দ্রুত হয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাস যেমন আমাদের কাছে আচানক হয়, তেমনি রাজনৈতিক স্থবিরতা কাটাতে শিক্ষার্থীদের তৎপরতাও আচানক ছিল না। আইয়ুব খানের আমলে বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন তৎকলীন রাজনৈতিক স্থবিরতাকে কাটিয়ে দিয়েছিল; এরশাদের আমলে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন রাজনৈতিক দলগুলোকে দিশা দিয়েছিল। তবে আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াতে রাষ্ট্রীয় সহিংসতার হিসাব আমলে নিয়ে বলা যায়, কেবল মুক্তিযুদ্ধকালের যুদ্ধাবস্থা ব্যতীত আর কোনো আন্দোলনে এত রক্ত ঝরেনি। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় ৬১ জনের মতো লোক প্রাণ হারিয়েছিলেন। এবার, আন্দোলনের মূল ২০ দিনে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হামলায় প্রায় ৮০০ জনের বেশি লোক প্রাণ হারিয়েছেন। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। যে আইয়ুব শাসনামলকে পুরো জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা চরম নেতিবাচক ও ন্যক্কারজনক হিসেবে উপস্থাপন করে এসেছে, সেই আইয়ুবের পুলিশ-সেনাবাহিনী চূড়ান্ত অবস্থাতেও এত লোককে গুলি করে হত্যা করতে পারেনি। কিন্তু, বাংলাদেশে হরদম মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাম-জপনেওয়ালা দল নির্বিচারে এই হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে।
এই প্রবন্ধে প্রধানত অভ্যুত্থানের সহিংসতার দিকটি আলোচনা করা হবে। প্রথমত, আন্দোলন কি সহিংস ছিল, নাকি অহিংস ছিল? নাগরিক আন্দোলনের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এবং আন্দোলনের নানাবিধ বর্গের কোথায় জুলাই অভ্যুত্থানকে স্থান দেওয়া যেতে পারে? দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও এর রাষ্ট্রীয় বয়ানের ধরন কেমন ছিল? তৃতীয়ত, অভ্যুত্থান-পরবর্তী সহিংসতা ও মবলিঞ্চিং/ভায়োলেন্সকে কীভাবে আলোচনা করা যেতে পারে? এবং চতুর্থত, এই সহিংস কর্মকাণ্ডকে কীভাবে বিচারের আওতায় আনা যেতে পারে, যেন জনগোষ্ঠী হিসাবে ইনসাফ কায়েম করা সম্ভব হয়?
আন্দোলনের ধরন : অহিংস ও সহিংসতার বিভাজন (ডাইকোটোমি) ছাড়িয়ে?
জুলাই গণ-অভ্যুত্থান যে দুটো আন্দোলনের সরাসরি উত্তরাধিকারী – ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন ও নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন – তার ধরন, অন্তত কেতাবি ভাষায় বলতে হয়, অহিংস ছিল। এমনকি, বিগত দশ বছর যাবত বিএনপি যত আন্দোলন করেছে, সেখানে রাষ্ট্রীয় নানাবিধ উষ্কানি থাকা সত্ত্বেও সহিংসতা থেকে নিজেদের দূরে রাখার যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা, তাতে কৌশল হিসাবে অহিংস নাগরিক অনানুগত্য বা সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্সকেই কৌশল হিসাবে গ্রহণের নজির ধরা পড়ে। এখন জুলাই মাসেও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন যখন মাঠে গড়ায় তখনও সেটার পন্থা, যেমন- রোডব্লক, সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদি, মোটাদাগে অহিংসের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু একটা সময় পর যখন, প্রধানত রাষ্ট্রীয় সহিংসতা প্রতিরোধে আন্দোলনে জ্বালাও-পোড়াও হাজির হলো, তাতে এই প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে আমাদের জন্য: তাহলে আন্দোলনের ধরন কেমন ছিল? অহিংস নাকি সহিংস? আর, এই সহিংস বা অহিংস আন্দোলন বলতে আদতে দুনিয়াতে কী বোঝানো হয়ে থাকে?
দীর্ঘদিন যাবত সহিংসতাকে (ভায়োলেন্স) অভ্যুত্থান ও বিপ্লবের সর্বাধিক জরুরি অনুষঙ্গ বলেই বিবেচনা করা হয়েছে। উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনসমূহ কেন অনিবার্যরূপে সহিংসতাতেই পর্যবসিত হয় বা শ্রেণি সংগ্রাম কেন সহিংস হয়ে উঠতে বাধ্য, তা নিয়ে প্রচুর তত্ত্বকথা তৈরি হয়ে আছে। খোলা চোখে দেখলে, ধ্রুপদী যে বিপ্লবগুলোর কথা আমরা স্মরণ করি বা কল্পনা করি, তার সবই ছিল সশস্ত্র লড়াই। আন্দোলন বা বিপ্লব বা অভ্যুত্থানে সহিংসতা ছাড়া সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়, প্রায় সবক্ষেত্রেই এমন ভাবনার প্রাধান্য ছিল। আমাদের মতো দেশে, যেখানে দীর্ঘদিনের সশস্ত্র বামপন্থী রাজনীতির ঐতিহ্য রয়েছে, সেখানে তো এই ভাবনার বাইরে আসলে খুব একটা আলোচনাই নেই, যদিওবা আমাদের ইতিহাসের চর্চিত অধিকাংশ আন্দোলনের ধরন ছিল ‘অহিংস’।
ইতিহাসে অহিংস আন্দোলনের নজির দীর্ঘ হলেও, খুব বেশিদিন হয়নি বিদ্যায়তনিক জগতে এ নিয়ে আলোচনা শুরুর। উনিশ শতকে হেনরি ডেভিড থরো১ বা বিশ শতকের হাওয়ার্ড জিন২ নৈতিক জায়গা থেকে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স বা গণ-অনানুগত্যের কথা বলেছেন, অন্যদিকে জিন শার্প৩ কৌশলের জায়গা থেকে দীর্ঘদিন যাবত এই ধরনের অহিংস আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। হাল জমানার গবেষকগণ খেয়াল করেছেন যে, পৃথিবীতে অহিংস প্রতিরোধ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরিখা চেনোওয়েথ ও স্টিফেন তাদের এক কাজে প্রায় একশ সহিংস ও অহিংস আন্দোলনের হিসাব কষে দেখালেন যে, ৫২ শতাংশ অহিংস আন্দোলন সফলতার মুখ দেখেছে, অন্যদিকে সহিংস আন্দোলনের ক্ষেত্রে সে হার মাত্র ২৬ শতাংশ৪। এখন এখানে সহিংস আন্দোলন বলতে বোঝানো হচ্ছে, যেখানে আন্দোলনের নীতি ও কৌশল হিসেবে সহিংসতা বা ভায়োলেন্সকে গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে অহিংস হচ্ছে, যেখানে আন্দোলনের নীতি ও কৌশল হচ্ছে প্রাণহানি রোধ বা হ্রাস করা; ফলে এখানে সহিংসতাকে পরিহার করে নিরস্ত্র বিভিন্ন কায়দা কানুন – যেমন, সমাবেশ, হরতাল, ধর্মঘট, বয়কট, অসহযোগিতা ইত্যাদি- ব্যবহার করা হয়। যারা অহিংস আন্দোলনের পক্ষে ওকালতি করেন, তারা এও দেখিয়েছেন বা বলেনও যে, প্রাতিষ্ঠানিক ইতিবাচক পরিবর্তনে সহিংস আন্দোলনের চেয়ে অহিংস আন্দোলনের প্রভাব বেশি।৫
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোনো আন্দোলনকে কি পুরোপুরি অহিংস বা সহিংস এই ভাগে ভাগ করে ফেলা সম্ভব? অহিংস আন্দোলনের মধ্যে কি সহিংসতা থাকতে পারে না? যেমন-- বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যা দেখা গেলো, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, নেতৃস্থানীয়দের বাসাবাড়ি ও পুলিশের থানায় লুট ও অগ্নিসংযোগ। এগুলোকে কী সহিংস নাকি অহিংস হিসাবে চিহ্নিত করা হবে? কেউ কেউ এগুলোকেও সহিংসতা বলেছেন। আবার কেউ কেউ এই নজিরগুলোকে ‘সহিংস’ বললেও আন্দোলনের কৌশল হিসাবে যেহেতু এসব মানুষের জানের ওপর হামলা করেনি বা একে মূল কৌশল হিসাবে চিহ্নিত করেনি; তাই এ আন্দোলনকে সহিংস বলতে নারাজ। অহিংস ও সহিংস এই বর্গের শিথিলতার কারণে সাম্প্রতিক গবেষকগণ একটু ভিন্নভাবে আন্দোলনগুলোকে বর্গায়িত করে : নিরস্ত্র প্রতিরোধ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ।৬ এখানে ‘সশস্ত্র প্রতিরোধ’ বলতে কি বুঝাচ্ছে, তা সহজেই অনুমেয়; সহিংস আন্দোলনের সংজ্ঞাতে যা বলা হয়েছিল সেটাই ছিল সশস্ত্র প্রতিরোধ। অন্যদিকে ‘নিরস্ত্র প্রতিরোধ’ এর মধ্যে পড়ে অহিংস প্রতিরোধ এবং নিরস্ত্র গণসহিংসতা (আন-আর্মড কালেক্টিভ ভায়োলেন্স)। অহিংস প্রতিরোধ হচ্ছে সমাবেশ, হরতাল, বয়কট ইত্যাদি, যেখানে প্রাণহানি বা ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোই মূল কথা। অন্যদিকে নিরস্ত্র গণসহিংসতা হচ্ছে নিরস্ত্র জনতার সামষ্টিক কর্মকাণ্ড, সেখানে ভাঙচুর, সম্পত্তি ধ্বংস করা, রাস্তায় ইটপাটকেল ছোড়া, অগ্নিসংযোগ করা ইত্যাদি থাকবে; কিন্তু সামরিক অস্ত্র বলতে যা বোঝায়, তার ব্যবহার থাকবে না। জনগণ অনেকটা খালি হাতে যে লড়াই চালায়, সেটাই এর আওতাভুক্ত। ফলে, সহিংস ও অহিংস আন্দোলনের এই দুই বর্গকে প্রতিস্থাপন করা হয় নিরস্ত্র ও সশস্ত্র এই দুই বর্গ দিয়ে। অহিংস আন্দোলনকে নিরস্ত্র আন্দোলনের অংশবিশেষ হিসাবে যেমন চিহ্নিত করা হয়, তেমনি নিরস্ত্র প্রতিরোধকে কখনো কখনো অহিংস আন্দোলনের সাথে সমার্থক হিসাবেই তুলে ধরা হয়।
এই আলোচনাতে আরেকটা প্রশ্ন অবধারিতভাবে চলে আসে, একেবারে অহিংস আন্দোলনে কখন সহিংস উপাদান যুক্ত হয়? অহিংস প্রতিরোধ কখন নিরস্ত্র গণসহিংসতার দিকে ধাবিত হয়? গবেষকরা মনে করেন, আন্দোলন অহিংস থেকে সহিংসতার দিকে যাত্রা করে প্রধানত রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে। ইতিহাসে সহিংস আন্দোলন থেকে অহিংস আন্দোলনের রূপান্তরের নজির যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে অহিংস আন্দোলনের সহিংস হয়ে উঠার নজির। সেটা সশস্ত্র না হলেও, আমরা উপরে যা নিরস্ত্র গণসহিংসতা হিসাবে চিহ্নিত করেছি, সে দিকে ধাবিত হয়। রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের নির্মমতা যেভাবে অহিংস আন্দোলনকে সহিংস করে তোলে বা সহিংস হতে বাধ্য করে, তেমনি আন্দোলনে সমাজের কত বিচিত্র শ্রেণি ও রাজনৈতিক শ্রেণি যুক্ত হয়েছে, তার ওপর নির্ভর করে সেই মাত্রাটা। আন্দোলন যত স্বতঃস্ফূর্ত হয়, তাতে নিরস্ত্র গণসহিংসতার দিকে ধাবিত হওয়ার ঝুঁকিও তত থাকে। আগেই উল্লেখ করেছি, এই ‘সহিংসতা’ র মাত্রা নিয়ে গবেষকগণের মধ্যে বিস্তর মতবিরোধ রয়েছে। লুটপাট বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতিকে কেউ কেউ ‘সহিংস’ উপাদান বললেও, অনেকেই এটাকে ‘অহিংস’ বলেই রায় দেন। এরিখা মনে করেন, এটা আন্দোলনের কৌশলের ওপর নির্ভর করে।
অহিংস আন্দোলনের এমন ‘সহিংস’ উপাদানের প্রভাব কেমন হতে পারে, এ নিয়েও দুটো মত রয়েছে। একপক্ষ মনে করেন, এটা দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলনে ক্ষতি করে কারণ তা রাষ্ট্রীয় নিপীড়নকে জায়েজ করে তুলতে পারে। অন্যদিকে, আরেকপক্ষ মনে করে, এই ধরনের নিরস্ত্র গণসহিংসতা দিনশেষে ফলদায়ক। ২০১১ সালের মিসরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কেউ কেউ দেখিয়েছেন, এই ধরনের সহিংসতা – যেমন পুলিশের থানা লুট বা অগ্নিসংযোগ – আন্দোলনকে বেগবান করেছিল। এক হিসাব মতে, ২০১১ সালে মিসরে আরববসন্তকালে প্রায় ৪০০০ পুলিশের যানবাহন এবং ২৫ শতাংশ থানাতে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছিল। কায়রোতেই প্রায় ৫০ শতাংশ থানা লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের শিকার হয়েছিল। তারা বলছেন, এই ধরনের সহিংসতা দিনশেষে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন কমাতে সাহায্য করেছিল, ফলে এটা অহিংস আন্দোলনের বিপরীতে না গিয়ে এটাকে আরও বেগবান করেছিল। পাশাপাশি, আরেকদল গবেষক দেখিয়েছেন, স্ট্রিট ফাইটিং বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির মতো নিম্ন মাত্রার সহিংসতা (লো-লেভেল ভায়োলেন্স) রাজনৈতিক উদারনৈতিকতার (পলিটিক্যাল লিবারেলাইজেশন) সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এমনকি, এই ধরনের লড়াই বা সহিংসতা এক্টিভিস্ট বা রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে আবেগ সঞ্চার করে, এক ধরনের রাজনৈতিক প্রতাপের অনুভূতি প্রদান করে। ৭
উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে দেখলে, আমরা দেখব, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পুরোদমে অহিংস আন্দোলন ছিল। শেখ হাসিনা আন্দোলনকারীদের রাজাকার বলে গালি দেওয়ার পর আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠে। আওয়ামীলীগের মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের যখন ছাত্রলীগকে আন্দোলন দমানোর খোলা আহ্বান জানালেন, তখনই প্রথম আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালানো হলো। এরপর সেই হামলাতে যুক্ত হয়েছে পুলিশ ও বিজিবি। পুলিশের গুলিতে একদিকে যেমন রাজপথ রক্তাক্ত হচ্ছিল, তেমনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছাত্র-জনতা প্রতিরোধও গড়ে তুলেছিলেন। পুলিশি নিপীড়ন, ক্রসফায়ার, গুম, অবিচার, দুর্নীতি, লুট, পাচার, বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিসহ আওয়ামীলীগ জমানার নানাবিধ অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে জমে থাকা দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ছিল এই প্রতিরোধ। পুলিশের আক্রমণের তীব্রতার সাথে জনতার প্রতিরোধও শক্ত হচ্ছিল। সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে ও স্থাপনাতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। আওয়ামীলীগ যে সকল স্থান, নিদর্শন বা প্রতীক ব্যবহার করে দিনের পর দিন দুর্নীতিকে জায়েজ করেছে, গণতান্ত্রিক যাত্রাকে রুদ্ধ করে কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠতে এস্তেমাল করেছে, সেগুলোর প্রতি জনতার আক্রোশ পড়েছে সর্বাধিক। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাকে যেমন আগুন দেওয়া হয়েছে, তেমনি আন্দোলনের মুহূর্তে বিভিন্ন থানাতে আগুন দেওয়া হয়েছে, রাজপথে খালি হাতে পুলিশের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছে সাধারণ জনগণ। অর্থাৎ, রাষ্ট্রীয় সহিংসতার মুখোমুখি হয়ে আন্দোলনে সহিংস উপাদান যুক্ত হয়েছে, যাকে আমরা বলছি নিরস্ত্র গণসহিংসতা। এতে রয়েছে রাজপথ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাতে অগ্নিসংযোগ, পুলিশের দিকে ইটপাটকেল ছোড়া, পুলিশকে ধাওয়া দেওয়া, থানায় হামলা করা এবং আন্দোলনের শেষের দিকে ক্ষমতাসীনদের প্রতিষ্ঠান ও বসতবাড়িতে লুট ও অগ্নিসংযোগ। এই ধরনের সহিংসতা আমাদের মিডিয়া বা গণপরিসর আচানক হিসাবে ঠাহর করলেও – জুলাই মাসের পত্রিকায় ধ্বংসযজ্ঞের অজস্র বিবরণ বিবেচনায় নিলে – সাম্প্রতিক গণ-আন্দোলনের ইতিহাসে মোটেও আচানক কিছু নয়। ২০০৬-২০২০ সালের মধ্যে পৃথবীতে যত আন্দোলন দেখা যায়, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রধান কারণ ছিল। পাশাপাশি, আন্দোলনের পদ্ধতি পুরোদমে অহিংস হলেও, প্রায় ২০ শতাংশ ক্ষেত্রে ভাঙচুর ও লুটপাট হয়েছে।৮ ফলে, কেবল বাংলাদেশেই নয়, এটা সারা দুনিয়ার গণ-আন্দোলনের খুব সাধারণ উপাদান। প্রশ্ন করা উচিত ছিল, কেন অহিংস আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় সহিংসতা দেখা দিলো?
রাজপথে ‘জ্বালাও-পোড়াও’ ও রাজনীতির নির্মাণ
বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাতে আগুন কারা দিয়েছে তা নিয়ে প্রচুর আলাপ-আলোচনা জুলাই মাসজুড়ে রাজনৈতিক মহলে ঘুরপাক খেয়েছে। কিছু কিছু স্থানে আগুন দেওয়ার সাথে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীরাই জড়িত বলে সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছিল। অন্যদিকে, তড়িৎগতিতে যেভাবে কিছু কিছু স্থাপনার ভাঙচুরকে সিনেম্যাটিক স্টাইলে (কল্পনা করুন ভাঙ্গা গ্লাসের সামনে বসে শেখ হাসিনার বক্তব্য) প্রপাগান্ডার হাতিয়ার বানানো হয়েছে, তাতে খোদ আওয়ামীলীগের দিকেই ভাঙচুরের আঙ্গুল তোলার অবকাশ ছিল বলে অনেকেই মনে করেন। আবার কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন, কেন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হলো না? এটা কারা করেছেন বা কে দায়ী, এই ধরনের আলোচনাতে যাচ্ছি না, আমি উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে ধরে নিচ্ছি, আন্দোলন চলাকালে রাষ্ট্রীয় সহিংসতার বিপরীতে এটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই ছিল।
এসব কিছুর গুরুত্বকে আমলে নিয়েই আমি বরঞ্চ যে বিষয়টা নিয়ে অস্বস্তি প্রকাশ করছি সেটা হচ্ছে, অভ্যুত্থানকালীন সহিংসতা ও জ্বালাও-পোড়াও বিষয়ক বয়ান। সরকারি মহল থেকে শুরু করে বিদ্বৎসমাজ পর্যন্ত বলা শুরু করেছেন, আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা, কিন্তু এই ধরনের জ্বালাও-পোড়াও-ভাঙচুর করছেন শিক্ষার্থীদের কাঁধে সওয়ার হয়ে, ‘আন্দোলনের নামে’ , কিছু দুষ্কৃতিকারী অথবা তৃতীয়পক্ষ (আওয়ামী বয়ান অনুযায়ী এই তৃতীয় পক্ষ হচ্ছে তাদের বিরোধী রাজনৈতিক দল, আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, বিএনপি ও জামায়াত-ই-ইসলামী)। সে ভাষ্য অনুযায়ী, শিক্ষার্থীরা ‘কোমলমতি’ , ফলে তারা এই ধরনের সহিংসতায় যোগ দিতে পারেন না, এবং সরকার আসলে এসব দুষ্কৃতিকারীদেরকে দমন করেছে, শিক্ষার্থীদের সাথে তাদের কোনো বিরোধ নেই। এমনকি, খোদ মাহফুজ আনাম জুলাই মাসের ২৬ তারিখ যে প্রবন্ধ লিখেছেন, সেখানে আন্দোলনের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছেন। সরকারকে প্রশ্ন করেছেন, আমরা কী আমাদের ভুল থেকে কিছুই শিখছি না? অথচ তিনি শুরুতেই বলেছেন : At the outset, we want to express our unambiguous condemnation of the mayhem created by ideologically and politically motivated groups whose aim was to destabilize our country, use the general discontent to instigate violence, and try to "topple the government"—as claimed by some ministers and which, if true, we vigorously denounce. This has made us realize that our country faces internal enemies opposed to our development and overall success. The destruction of public property and the setting of fire to essential government offices, transport facilities and part of internet infrastructure that greatly crippled trade, manufacturing and the daily life of citizens need to be highly condemned, and the perpetrators exposed and punished within the law. We in the media will assist the government in unearthing this move against Bangladesh. Those who opposed our birth in 1971 must be resisted, defeated and destroyed.৯
ধ্বংসযজ্ঞ, অগ্নিসংযোগ নিয়ে সরকার যা বলছিল, তার সবচেয়ে পরিশীলিত রূপ পাওয়া যাচ্ছে মাহফুজ আনামের লেখাতে। তিনি সরকারি বক্তব্য অনুসারে একাত্তর সালকেও এখানেই নিয়ে এসেছেন, এবং একাত্তরের বিরোধীদের প্রতিরোধ, পরাজিত ও ধ্বংস করে ফেলার প্রতিশ্রুতিও জানিয়েছেন।
কিন্তু, এই যে অগ্নিসংযোগ লুটপাট বা জ্বালাও পোড়াও দেখে আতকে উঠলেও, ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে, পাকিস্তান আমলে যতগুলো আন্দোলন ও অভ্যুত্থানের উল্লেখ মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবশালী ইতিহাসচর্চাতে পাওয়া যায়, সেগুলোতেও এই ধরনের ‘জ্বালাও-পোড়াও’ অত্যন্ত সাধারণ প্রবণতা ছিল। শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নেমেছেন, সরকার বাঁধা দিয়েছে, ফলস্বরূপ, জ্বালাও-পোড়াও শুরু হয়েছে। আমাদের ইতিহাসে এমন কোনো আন্দোলন পাওয়া যাবে না, যেখানে জ্বালাও-পোড়াও ধরনের ঘটনা ঘটেনি। যেমন, ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর নিয়ে সরকারি প্রেসনোটটা দেখেন : ‘গতকল্য সকাল হইতেই ঢাকা শহরের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামা শুরু হয়। হাঙ্গামাকারী ও হুজুগ-প্রিয় তরুণদের সহিত মিলিত হইয়া ছাত্রগণ রাস্তায় চলাচলকারী প্রত্যেকটি গাড়ির গতিরোধ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে দুষ্কৃতিকারিগণ ছাত্রদের সহিত মিলিত হয় এবং হাঙ্গামা শুরু করে।’১০
উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান যে ‘শান্তিপূর্ণ’ ছিল না তা তো প্রায় সকল ইতিহাসবিদই বিভিন্নভাবে আমাদের জানিয়েছেন। মওলানা ভাসানীকে নিয়ে সে সময় টাইম ম্যাগাজিন প্রতিবেদন ছাপিয়েছিল ‘প্রফেট অফ ভায়োলেন্স’ নামে। সম্প্রতি মহিউদ্দিন আহমদ এক লেখাতে জানাচ্ছেন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কালে ‘ঢাকায় তিন–চারজন মন্ত্রীর বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছিল, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান যে গেস্টহাউসে ছিলেন, সেখানে আগুন দেওয়া হয়েছিল, দৈনিক পাকিস্তান ও মর্নিং নিউজ–এর অফিসে আগুন দেওয়া হয়েছিল’ । হায়দার আকবর খানের বিবরণীটা পড়ে দেখুন : ‘মার্চ মাসে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন গ্রামের দিকে ছড়িয়ে পড়ল। কয়েকটি থানায় জনগণ আক্রমণ করে বন্দুক লুট করে। কিন্তু তেমন ঘটনা খুব বেশি নয়… গ্রামে গ্রামে তহশিল অফিসে জনগণ আগুন দেয়। … কয়েকট অঞ্চলে গরুচোরদের ধরে অথবা সাধারণভাবে খুব ঘৃণিত ব্যক্তিদের ধরে প্রকাশ্যে গণআদালত করে বিচার করে জবাই করা হয়েছিল’।১১ এই তাৎক্ষণিক বিচার নিয়ে তৎকালে দি গার্ডিয়ান লিখেছিল : ‘There are reports of setting up in parts of Pakistan of ‘People's courts’ which were meting out instant executions to score of wrong doers before mobs of widely applauding peasants.’১২
এমনকি, বর্তমানে শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে সরকারি বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত এই জ্বালাও-পোড়াওকে ‘হত্যাযজ্ঞে’ র প্রিটেক্সট হিসেবে উল্লেখ করছেন, তার সাথে একাত্তরের সালের ইয়াহিয়া খানসহ পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের বক্তব্যের হুবহু মিল রয়েছে। ২৬ শে মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণ থেকে শুরু করে পুরো নয় মাস পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ পঁচিশ মার্চের ক্র্যাকডাউনের প্রিটেক্সট হিসেবে মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনে আওয়ামীলীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ‘ধ্বংসযজ্ঞ’ ও ‘আইন-অমান্য’ কে হাজির করেছে। এমনকি, নব্বইয়ের গণআন্দোলন বা নব্বই পরবর্তীতে শেখ হাসিনার বিভিন্ন আন্দোলনে রাজপথের জ্বালাও-পোড়াও ছিল অতীব সাধারণ ঘটনা।
মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের আন্দোলনের ইতিহাসের আলোকে যদি আমি জুলাই অভ্যুত্থানকে বিবেচনায় নেই, তাহলে রাষ্ট্রীয় সহিংসতার প্রতিক্রিয়ায় এই ‘জ্বালাও-পোড়াও’ মোটেও কোনো নতুন ঘটনা (ফেনোমেনোন) নয়। আমাদের ইতিহাসে, সেই ঔপনিবেশিক আমল থেকেই, আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে রাজপথে নামা এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়ার বিপরীতে ‘সহিংস’ হয়ে উঠা, একেবারে ‘রাজনীতি’ নামক বিষয়টার সাথেই জড়িত। আমি বলছি না যে, ‘জ্বালাও-পোড়াও’ -ই গণঅভ্যুত্থান, বরঞ্চ বলছি, জনগণের অসন্তোষ যখন গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দেয়, তখন সেখানে এই ধরনের সহিংস উপাদান থাকেই। অন্তত ইতিহাস আমাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছে। ভারতবর্ষে ‘রাজনীতির নামে’ এই ধরনের আইনভঙ্গের সহিংস ঘটনা নিয়ে দীপেশ চক্রবর্তী যেমন বলছিলেন, ‘The incidents are a large part of what takes place today not just in ‘the name of politics’ but rather as the very stuff of politics itself’.১৩
যেকোনো আন্দোলনকে ‘নিয়মতান্ত্রিক’ বলে দেখানোর একটা অদ্ভূত খায়েশ প্রায় সকল মহলেই ভর করে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মতো ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন ‘নিয়মতান্ত্রিক’ হতে পারে না। এখানে ‘নিয়মতান্ত্রিক’ মানেই হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় বয়ানের ভেতরে গিয়ে তার কোলে বসে আন্দোলনের ভনিতা করা। বাংলাদেশে বর্তমানে ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থাতে যেখানে ন্যূনতম নির্বাচনের মাধ্যমে রেজিম বদলের সকল পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তখন ‘নিয়মতান্ত্রিক’ পথে আন্দোলন মানেই হচ্ছে রাষ্ট্রের বাতলে দেওয়া পথে আন্দোলন করা। আর যাই হোক, বিদ্যমান রাষ্ট্র ও ক্ষমতাকাঠামো পরিবর্তনের লড়াই রাষ্ট্রীয় বাতলে দেওয়া ‘নিয়মতান্ত্রিক’ পথে হওয়ার কথা ছিল না। উপরন্তু, কোনো জনগোষ্ঠীকে যখন সহিংস কায়দায় শাসন করা হয়, তখন জনগোষ্ঠীর অভ্যুত্থানের মধ্যেও ‘নিয়মবহির্ভূত’ সহিংস উপাদান জড়িত হয়ে পড়ে।
রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও ‘নতুন’ বয়ান
আন্দোলনকালে রাষ্ট্রীয় সহিংসতা এক নতুন স্তরে প্রবেশ করলেও, আওয়ামী জমানার রাষ্ট্রীয় অপরাপর সহিংসতা থেকে ভিন্নভাবে এটা পাঠ করা সম্ভব নয়। এই রেজিমের সহিংসতাকে বোঝা যাবে তিনটা জিনিস দিয়ে : গুম, ক্রসফায়ার বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও গায়েবি মামলা। অর্থাৎ, আইনি ও বে-আইনি – এই দুই তরিকার সহিংসতা দিয়েই বোঝা যাবে, কীভাবে আওয়ামীলীগ বাংলাদেশের গণপরিসর থেকে রাজনীতি ও সম্ভাবনাকে গায়েব করে দিয়েছিল। আমরা একে চিহ্নিত করেছিলাম ‘মারণ-রাজনীতি’ (নেক্রোপলিটিক্স) নামে।১৪ আশিলে এম্বেম্বের ধারণা ব্যবহার করে আমরা বলেছিলাম যে, এ ধরনের রাষ্ট্রপ্রণালীতে আইনের শাসন, সহিংসতা এবং জরুরি অবস্থার ফারাক ঘুচে একাকার হয়ে যায়। জৈবরাজনৈতিক রাষ্ট্রে যেখানে মানুষের জীবন সার্বভৌম রাজনীতির কেন্দ্রীয় বিষয় অর্থাৎ রাজনৈতিক কলাকৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিণত হয়, মারণ-রাজনৈতিক রাষ্ট্রে মউত হয়ে দাঁড়ায় সার্বভৌম ক্ষমতার প্রধান চরিত্র। অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষের জীবনকে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে এনে সার্বভৌমত্বের ব্যতিক্রমী ক্ষমতার অংশ হিসেবে ‘হত্যাযোগ্য’ প্রাণ তৈরি করার শাসনপ্রণালী এ নয়; বরং কাঠামোগত হত্যাযজ্ঞকে শাসনপ্রণালীর অনিবার্য অনুষঙ্গে পরিণত করার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বন্দোবস্তই মারণ-রাজনীতি। এ ধরনের রাজনৈতিক বন্দোবস্তে পাইকারি হারে (large scale death) মউত উৎপাদন করাই সার্বভৌম ক্ষমতার প্রধান কাজ। কাজেই মারণ-রাজনীতির মানে হলো মউতের দোর্দণ্ডপ্রতাপের কাছে জীবনের পরাজয় (subjugation of life to the power of death)। একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী যেখানে জীবন নামক অপেক্ষাগারে মৃত্যু নামক ট্রেনে ওঠার অপেক্ষায় থাকে। এরকম রাজনৈতিক বাস্তবতায় মৃত্যুই ‘নিয়ম’ , জীবন ‘ব্যতিক্রম’ । নজিরবিহীন রাষ্ট্রীয় জুলুম-সহিংসতা এবং সেই সহিংসতা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জালের মতো বিস্তার ঘটানো, যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধসম পরিস্থিতি বজায় রাখা, উন্নয়নের নামে প্রাণ-প্রকৃতির ব্যাপক মাত্রার লুন্ঠন-ধ্বংস-উচ্ছেদ, খুন-খারাবির নানাবিধ শর্ত বিরাজমান থাকা ও কনসেনন্ট্রেশন ক্যাম্প, ঘেটো, ছিটমহল; ‘মানুষ’ ধারণার শ্রেণিগত ও কর্তৃত্বক্রমতান্ত্রিক স্তরবিন্যাস (মানুষ আর ‘হীন’ মানুষের পৃথকীকরণ)- হচ্ছে বাংলাদেশের মারণ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার কিছু অনিবার্য চিহ্ন।
যেভাবে জরুরি অবস্থার মতো আপদকালীন ব্যবস্থাকে এখানে ‘স্বাভাবিক’ নিয়মে পরিণত করা হয়েছে, সাংবিধানিক শর্তের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা হয়েছে মৌলিক অধিকারের মতো নিঃশর্ত মানবীয় অধিকার, ক্রসফায়ারের মতো নৃশংস খুনের আইনগত ভিত্তি দেওয়া হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনি সন্দেহ/মনে হওয়ার ভিত্তিতে যেভাবে নাগরিকের দেহতল্লাশি থেকে শুরু করে বাসা-বাড়িতে বিনা পরোয়ানায় অনুপ্রবেশের অধিকার (প্রয়োজনে দরজা ভেঙ্গে) সংরক্ষণ করে, তার নজির গোটা দুনিয়ায় বিরল। এরকম জৈবিক ও রাজনৈতিক অধিকারহীন নাঙ্গা জীবনযাপন করে বাংলাদেশের মানুষ। তারজন্য এমনকি সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যতিক্রমের কোটায় পড়বার প্রয়োজন পড়ে না। রাষ্ট্রীয় বর্ণবাদী একচেটিয়া সার্বভৌম ক্ষমতার কাছে এরকম উন্মোচিত নাঙ্গা জীবনের অধিকারীরাই আবার সমাজের জাতিগত-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক-লৈঙ্গিকভাবে ভিন্নধর্মীদের ‘অপর’ বর্গে চিহ্নিত করে, বর্ণবাদী সার্বভৌম ক্ষমতার মতাদর্শ সমাজে পুনরুৎপাদন করে এবং সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জালের মতো বিস্তার ঘটায়। ফলে নাস্তিক-শিবির-সমকামী এমনকি রাজনৈতিক অধিকারের জন্য লড়াইরত নাগরিকও সার্বভৌম ক্ষমতার ‘অপর’ ও বধযোগ্য প্রাণ হিসেবে উন্মোচিত হয়।
বিগত পনের বছরে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর খায়েশের ওপর যে নাগরিকের হায়াত-মউত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল, তার চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে জুলাই মাসের ম্যাসাকার। আওয়ামী রেজিমের সামগ্রিক সহিংসতাকে টের না পেলে বোঝা যাবে না, কীভাবে একটা রাষ্ট্র তার হাজার খানেক লোককে মাত্র বিশদিনে স্রেফ রাস্তাতেই মেরে ফেলে! যে ধরনের মতাদর্শিক ও আইনি ব্যবস্থা দ্বারা এখানে বধযোগ্য প্রাণ তৈরি করা হয়েছে, এবং সিভিল সোসাইটি থেকে এর সম্মতি আদায় করা হয়েছে, সেটাই আসলে জুলাই মাসের নির্মম ম্যাসাকারে চূড়ান্ত রূপে হাজির হয়েছে। হত্যা করে লাশ পুড়িয়ে ফেলা বা নির্বিকার ভঙ্গিতে গুলি করা, বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সামনেই মোবাইলে দেখিয়ে ‘একটা মরলে আরেকটা দাঁড়ায়’ বলা – এগুলো সম্ভব হয়েছে এই দীর্ঘদিনের বাস্তবতায়।
তবে, আন্দোলনের বিশেষ মুহূর্তে এসে, রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও তাদের বয়ানের ক্ষেত্রে দুটো অভিনব বিষয় দেখা যায়। প্রথমত, নাগরিক আন্দোলন দমনে হেলিকপ্টার বা আকাশ পথের ব্যবহার, হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা প্রদানে বাঁধা প্রদান ও ছররা গুলিতে চোখ আক্রমণ করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সহিংসতার এক নতুন পর্বে বাংলাদেশ প্রবেশ করেছে। প্রথম আলো এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, কাঁদানে গ্যাস ও ছররা গুলিতে চোখে আঘাত পেয়ে ১৭ জুলাই–২৭ আগস্ট পর্যন্ত চিকিৎসা নেন ৮৫৬ জন। তাঁদের মধ্যে ৭১৮ জনকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়; চোখে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে ৫২০ জনের; দুই চোখ নষ্ট ১৯ জনের। এক চোখ নষ্ট ৩৮২ জনের। এই ধরনের ঘটনার নজির আমরা আরো দুটো অঞ্চলে দেখতে পাই : কাশ্মীর ও ফিলিস্তিনে। কাশ্মির নিয়ে ২০১৬ সালের একটি প্রতিবেদন দেখুন, ‘…doctors at Srinagar’ s Shri Maharaja Singh hospital have treated at least 446 patients with injuries sustained from being shot at with pellet guns, which have been used against protesters by Indian forces in the region.’১৫ একইভাবে ইসরায়েলি স্নাইপারদের দেখা যায় ফিলিস্তিনিদের চোখ বরাবর গুলি করতে।
দ্বিতীয়ত, বয়ানের ক্ষেত্রে, পাকিস্তান আমলে আমরা দেখেছি, সরকার রাষ্ট্রীয় সহিংসতার প্রিটেক্সট হিসেবে আন্দোলনকারীদের কর্মকাণ্ডকে হাজির করেছে। অর্থাৎ, দায়টা আন্দোলনারীদের ওপর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এবার আওয়ামীলীগের তরিকা ভিন্ন : তারা আন্দোলনকারীদের ‘কোমলমতি শিক্ষার্থী’ বলে ‘নিষ্ক্রিয় সত্তা’ বানিয়ে দিয়েছে। এক অদৃশ্য ‘তৃতীয় পক্ষ’ এই ‘নিষ্ক্রিয় সত্তাদের’ দের কাঁধে সওয়ার হয়ে জ্বালাও-পোড়াও করছে, ফলে এই হত্যাযজ্ঞের দায় সেই ‘তৃতীয় পক্ষে’ র। বর্তমানে যারা ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে একটু খোজ খবর রাখেন, তারা এই ধারার যুক্তির সাথে পরিচিত। ইসরায়েলি বাহিনী একইভাবে দাবি করে, তাদের আসল টার্গেট হামাস। কিন্তু হামাস যেহেতু সাধারণ ফিলিস্তিনিদের ‘হিউম্যান শিল্ড’ হিসেবে ব্যবহার করছে, সেহেতু হামাসকে নিধন করতে গিয়ে সাধারণ ফিলিস্তিনিরাও নিহত হচ্ছেন।১৬ আওয়ামীলীগের যুক্তিও একই ধারায় চলছে : যেহেতু অদৃশ্য ‘তৃতীয় পক্ষ’ কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাঁধে সওয়ার হয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে, সেহেতু তৃতীয় পক্ষকে দমন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা মারা যাচ্ছেন।
ফলে, এটাও এক ট্রাজেডি। রীতিমতো সশস্ত্র সংগ্রাম করে যে জনপদ স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করেছিল, যারা জন্মের মুহূর্তে ফিলিস্তিনবাসীর মুক্তির সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিল, সেই রাষ্ট্র আজকে ইতিহাসের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছিল। ফিলিস্তিনে গণহত্যাকারীদের কৌশল ও বয়ান দুটোই আত্মস্থ করে নিয়েছে এমন এক দল, যারা আবার মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে বলে এতদিন প্রচার করেছে।
অভ্যুত্থান-পরবর্তী সহিংসতা
অভ্যুত্থান পরবর্তী পর্যায়ে, অর্থাৎ হাসিনার পলায়নের পরপরই সহিংসতার আরেক ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশে। এতে যেমন থানা পোড়ানো, আওয়ামীলীগের নেতাদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, শেখ মুজিবের ভাস্কর্য ভাঙচুর ও আওয়ামীলীগের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও স্মৃতিতে অগ্নিসংযোগ রয়েছে, তেমনি রয়েছে হত্যাকাণ্ড, মবলিঞ্চিং এর ঘটনা। এর অধিকাংশকে আসলে সাম্প্রতিক হত্যাযজ্ঞের ‘প্রতিশোধ’ বা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে গণপরিসরে বিবেচিত হয়েছে। পাশাপাশি, মুজিবের ভাষ্কর্য ভাঙচুর ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নের ভাঙচুরকে এই দুটোর আওয়ামী ফ্যাসিবাদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে পড়ার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই দেখা হয়েছে। যদিও অনেকে এতে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অবস্থান বা ভাস্কর্য বিরোধী অবস্থানকে ফোকাস করেছেন, এগুলোও যে ছিল না, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এগুলোকে আওয়ামী শাসনামলের ‘ক্ষমতা’ র প্রতীকের ভাঙচুর হিসাবে দেখাটাই বেশি যৌক্তিক। যে মুক্তিযুদ্ধ বা যে মুজিব শেখ হাসিনার আওয়ামী রেজিমের ফ্যাসিবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন, এই ভাঙার মধ্য দিয়ে যেন তার মুক্তি ঘটেছে। ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে ভাস্কর্যের ভাঙচুর মোটেও আচানক কিছু নয়। অভ্যুত্থান বা বিপ্লব পরবর্তী দুনিয়াতে এটি হারহামেশাই হয়ে থাকে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে কলম্বাসের ভাস্কর্যের ওপর হামলাকে স্মরণ করা যেতে পারে।
পাশাপাশি, অভ্যুত্থান পরবর্তী পর্যায়ে নানা ধরনের সহিংসতাতে মানুষের অংশগ্রহণ যেন ছিল মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। কড়াইলের নিম্ন আয়ের বসতির এক বাসিন্দার জবানে যেন এই পুরো সহিংসতার রূপর ধরা পড়েছিল, ‘আফা, আমরার এলাকার নেতারে তো মাইনষে এমন মাইর দিছে, হে হের বউ–বাচ্চা লইয়া বাড়িঘর থুইয়া ভাগছে। এহন তো মাইর খাইবোই, এত দিন নেতাগিরি কইরা মাইনষের ট্যাহা মাইরা খাইছে আর দুতালা বিল্ডিং দিছে। এসি-মেসি লাগাইয়া কী বিশাল অবস্থা! এহন মাইনষে সুযুগ ফাইছে, এহন তো তারে মারবোই।’১৭
তবে, এর মধ্যেই সংখ্যালঘুরাও আক্রমণের শিকার হন, এবং এ নিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রপাগান্ডা পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করে তোলে। যদিও, এই হামলার অধিকাংশ, প্রায় সবই ছিল আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে জড়িতদের ওপর। কিন্তু এই পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়ে উঠে অভ্যুত্থান পরবর্তী ৩/৪ দিন পুলিশ প্রশাসনের অনুপস্থিতি। পুলিশ বিগত ২০দিন যে ম্যাসাকার চালিয়েছিল, তার ফলে অভ্যুত্থান পরবর্তী সকল ক্ষোভ তাদের ওপর পড়ে। ফলে, তারা থানা থেকে পালিয়ে যান, কর্মস্থলে যোগ দিতে চাননি। থানাগুলো শূন্য হয়ে পড়ে বাংলাদেশের। তখন যে ধরনের সহিংসতার আশঙ্কা করা হয়েছিল, তা অদ্ভূতভাবে রুখে দিয়েছিল আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী-জনতা। হঠাৎ করে বাংলাদেশের সমাজ যেন আবার সক্রিয় হয়ে উঠছিল। সহিংসতা, অপরাধ বা সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার আশঙ্কা থেকে মহল্লা, এলাকা, পাড়াতে সক্রিয়ভাবে পাহারা ও টহলের ব্যবস্থা করেন এলাকাবাসী ও শিক্ষার্থীরা। দিনের বেলাতে ট্রাফিক কন্ট্রোল করেন শহরগুলোতে। পুরো এক সপ্তাহ বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আদতে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন শিক্ষার্থীরা।
যেকোনো অভ্যুত্থান ও আন্দোলন রাজপথে গড়ায় মূলত ‘আইন’ কে ভঙ্গ করেই। জুলাই অভ্যুত্থান ও এর পরবর্তী পর্যায়ে আমরা এর চূড়ান্ত নমুনা দেখেছি। আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানো, এবং একই সাথে আইনের দায়িত্ব পালন করা – দুটোই ঘটেছে আইনি প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে। এর নেতিবাচক হালতও ধরা পড়েছে কিছুদিন পর। মব ভায়োলেন্স বা মব লিঞ্চিং শুরু হয়েছে। ‘জনতা’ দ্রুত ‘মব’ -এ রূপান্তর হয়ে যায়। তবে, বাংলাদেশে গণপিটুনি খুব একটা আচানক জিনিস নয়। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্য মতে, দেশে গত সাড়ে ছয় বছরে গণপিটুনিতে কমপক্ষে ২৮৬ জনকে হত্যা করা হয়েছে। একদিকে অভ্যুত্থানে আইন নিজের হাতে নেওয়ার প্রবণতা এবং অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পুরোপুরি কার্যকরী না হয়ে উঠা, মব ভায়লেন্স বা গণপিটুনি বা বিচারের ভার নিজের হাতে নেওয়ার প্রবণতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবেষকরা অন্যান্য স্থানের অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন, যখন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ন্যায়বিচার পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হতে থাকে ও প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্নীতিগ্রস্থ বলে জনমনে স্থায়ীভাবে জায়গা করে নেয় তখন সে সমাজে বিচারের নামে গণপিটুনি বা আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এমনকি, যখন লোকে মনে করে, রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ দুর্বল হালতে রয়েছে বা অক্ষম অবস্থায় রয়েছে, তখনও এটা বৃদ্ধি পেতে থাকে।১৮ ক্রসফায়ার বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে রাষ্ট্র যে তরিকায় জায়েজিকরণ করার চেষ্টা চালায়, সে একই তরিকার ফলাফল বা অংশ হচ্ছে গণপিটুনি। বাংলাদেশে বিগত দেড় দশকে ক্রসফায়ার বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের পক্ষে যে ধরনের সম্মতি উৎপাদন করা হয়েছে, এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে মব ভায়োলেন্সকে জায়েজ করার সম্মতিমূলক উপাদান।
ইনসাফ প্রশ্ন
বাংলাদেশ পুরো আওয়ামী রেজিম ও জুলাই-আগস্ট মাসে যে ধরনের সহিংসতা প্রত্যক্ষ করেছে, তার প্রভাব সুদূররপ্রসারী। রাষ্ট্রসংস্কারের জোর আলাপ চলছে। কিন্তু আমরা যদি এই হত্যাযজ্ঞের শিকার জনগোষ্ঠীকে ইনসাফ দিতে না পারি, তাহলে এই সহিংসতার চক্র চলতেই থাকবে। রাষ্ট্রের সংস্কার কোনো মতেই সম্ভব নয়। বর্তমানে যে অবস্থা চলছে তার আলোকে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা জরুরি। সম্প্রতি আওয়ামীলীগের একেবারে চিহ্নিত নেতাদের নামে যেসকল মামলা হচ্ছে, তা পুরোটাই হচ্ছে আওয়ামী কায়দায়। গত এক দশকে বিএনপিকে যেভাবে আওয়ামীলীগ দমন করেছে তার অন্যতম হাতিয়ার ছিল, ‘গায়েবি মামলা’। এমনকি মৃত ব্যক্তি অথবা ঘটনার দিন বিদেশ ছিলেন, অথবা ঘটনাই ঘটেনি, তবু মামলা দায়ের করা হয়েছে। এবং সে মামলাতে শত শত লোক গ্রেফতার করা হয়েছে। বিএনপির কোনো কোনো নেতার বিরুদ্ধে ৪০০/৫০০ এর মতো গায়েবি মামলা ছিল। গায়েবি মামলার হার এত বেশি ছিল যে, গত বছর নির্বাচনের প্রাক্কালে ফোরাম ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ শীর্ষক প্ল্যাটফর্ম থেকে ‘গায়েবি মামলা ও আগামী নির্বাচন’ নামে একটা ওয়েবিনারও আয়োজন করা হয়। সেখানে আসিফ নজরুল বলেছিলেন, ‘এই সরকারকে পুলিশ টিকিয়ে রেখেছে এমন কথাটা যে প্রায়ই শুনি, সেটা যতটা না হামলা করে তার চেয়ে বেশি মামলা করে’ । এই গায়েবি মামলাকে আমি বলছি আওয়ামী-কায়দা। বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের বিরুদ্ধে জিয়াউর রহমান সম্পর্কে ‘আপত্তিকর মন্তব্য’ করার মামলা দেওয়া হয়েছে। আমরা দীর্ঘ এক দশক লড়াই করেছি বাকস্বাধীনতার জন্য। এখন যারা আমাদের বাকস্বাধীনতাকে আটকে রেখেছিল, তাদেরকে এমন মামলা দিচ্ছি, যেগুলো আবার বাকস্বাধীনতার প্রশ্নের সাথেই সাংঘর্ষিক। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার মামলার সাথে জিয়াউর রহমানকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের মামলার ফারাক কোথায়?
তবে, ইনসাফ কয়েকটি জরুরি নোক্তা দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থায়। যারা/যিনি আবেদন করেছেন, তার সম্ভবত খুব ভালো করে জানার কথা যে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে যে হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে তাকে ‘গণহত্যা’ (জেনোসাইড) বলা যায় না। কেন বলা যায়, আমি খোলাসা করি। জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশের পুলিশ, বিজিবি, র্যাব, ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামীলীগের অন্যান্য সংগঠনের আক্রমণে যে হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে, তাকে জনপরিসরে ‘গণহত্যা’ বলা হচ্ছে। জনপরিসরের এমনতর ব্যবহার নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই। বাংলা ভাষায় ‘গণহত্যা’ শব্দের মধ্যে একের অধিক হত্যার একধরনের ইঙ্গিত থাকায় যখনই বহুলোকের হতাহতের ঘটনা ঘটে তখন সেই হত্যাযজ্ঞকে ‘গণহত্যা’ বলে অভিহিত করার প্রচলন আছে। রেটরিক হিসাবে যে গণহত্যা প্রচলিত আছে তা আসলে ইংরেজিতে ম্যাসাকার অর্থে। যদিও আমার মতে, এর বাংলা হিসাবে ‘হত্যাযজ্ঞ’ ব্যবহার করা যেতে পারে।
কিন্তু, Genocide এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবেও গণহত্যার ব্যবহার প্রচলন আছে। আমি যে অভিযোগের কথা পত্রিকায় দেখলাম, সেটা আসলে জেনোসাইডের অর্থে গণহত্যা। এখন গণহত্যা রেটরিক হিসেব ব্যবহার করলেও, আইনি ভাষায় এই ‘গণহত্যা’ র সংজ্ঞা আবার খুবই নির্দিষ্ট। এর মানদণ্ড খুব উঁচু। সম্প্রতি ফিলিস্তিনের যে গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েলি, তা নিয়ে বিতর্ক ও ইসরায়েলের যুক্তি শুনলেই আমরা টের পাবো।
গণহত্যার (জেনোসাইড) যে আইনি সংজ্ঞা তা খেয়াল করলে বোঝা যাবে, এই অপরাধের কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে ‘গোষ্ঠী’ বা গ্রুপ। এই অপরাধ সংঘটিত হয় কোনো একটা গ্রুপের বিরুদ্ধে। এটা এতটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী যে, মাত্র চারটা গোষ্ঠীকে আইনে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে : জাতিগত, নৃতাত্ত্বিক, বর্ণগত ও ধর্মীয় (নেশনাল, এথনিক্যাল, রেসিয়াল ও রিলিজিয়াস)। অর্থা, যদি এই চারটা গোষ্ঠীর কোনোটার অন্তর্ভুক্ত বলে কাউকে হত্যা বা আরও কিছু নির্দিষ্ট অপরাধ করেন, তাহলে সেটা গণহত্যা (জেনোসাইড) হয়। অবশ্য, ১৯৭৩ সালের ট্রাইব্যুনাল এখানে ‘পলিটিক্যাল’ গোষ্ঠীকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এখন জুলাই মাসে যা হয়েছে, তা কোনোভাবে কোনো উপর্যুক্ত নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বলে প্রমাণ করা যাবে না। এবং সেটা হয়ও নি। এই হত্যাযজ্ঞ বা ম্যাসাকার আইনি ভাষায় ‘গণহত্যা’ র অন্তর্ভুক্ত হয় না। বরঞ্চ, এখানে যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তা হলো মানবতাবিরোধী অপরাধ, ।
শেখ হাসিনা ও তার দলবলের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী যে অপরাধের অভিযোগ তোলা দরকার সেটাকে কেবল জুলাই মাসের হত্যাযজ্ঞের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। বরঞ্চ পুরো শাসনামলকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গুম, নির্যাতন, ক্রসফায়ারের মতো হত্যাকাণ্ড - সবই মানবতাবিরোধী অপরাধের ভেতরেই পড়ে। আওয়ামী শাসনামল গুম, খুন, ক্রসফায়ার, আয়নাঘরের মতো টর্চারসেলে নির্যাতন, জেল, পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু ইত্যাদি দিয়ে পনের বছরের ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। গুম ও ক্রসফায়ারের শিকার হয়েছিলেন কয়েক হাজার মানুষ। জেলে গিয়েছেন কয়েক হাজার রাজনৈতিক বিরোধী। কেবল গত নির্বাচনের পূর্বে বিএনপিরই হাজার বিশেক লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এরপর এসেছে জুলাই হত্যাযজ্ঞ। অর্থাৎ, আমি বলছি, হাসিনা ও তার দলবলের বিরুদ্ধে যখন মামলা করা হচ্ছে, তখন কেবল জুলাই মাসের হত্যাযজ্ঞকে ফোকাস করতে গেলে, সামগ্রিকভাবে পুরো রেজিমকে রেহাই দেওয়া হয়ে যাবে। অভিযোগ দাখিলের বেলাতে জনমতের চাপ এড়িয়ে ভালো করে ভেবেচিন্তে অভিযোগ তোলা দরকার, অন্তত আইনি বিষয়ে তো অবশ্যই। হরেদরে এমন অভিযোগ তোলা হলো, যা থেকে সহজেই রেহাই পেয়ে যায়; অথবা বড় অপরাধকে আমলে না নিয়ে ছোট অপরাধকে বড় করে তোলা হলো, যার ফলে কিছুদিন পর বিচারকার্যক্রম নিয়ে নোংরা রাজনীতি শুরু হয় যায়।
অন্যদিকে যে মামলাগুলো আইসিটিতে করা হচ্ছে, সেখানে আইসিটি নিয়েও কিছু প্রশ্ন তোলা দরকার। গতকাল দেখলাম, উম্মে ওয়ারা প্রথম আলোতে লিখছেন, যত গুম–খুনের বিচার আইসিটির মাধ্যমেই যুক্তিযুক্ত। তার সাথে একমত দ্বিমতের চাইতে গুরুতর বিষয় তিনি বলছেন, ‘শেখ হাসিনাসহ অন্যদের বিচার নিশ্চিত করতে হলে আইসিটি ট্রাইব্যুনালকে ঢেলে সাজিয়ে তার মাধ্যমেই করা উচিত’ । এই ঢেলে সাজানোর প্রশ্নে, আমাদের আগের অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি, আরেকটা সিরিয়াস বিষয়ে মনযোগ দিতে হবে।
দ্বিতীয়ত, আমি ট্রাইব্যুনালের একটা স্পেসিফিক বিষয়ের দিকে আলোকপাত করতে চাই। বিচার শুরুর আগে এসব আলাপ আমাদের তুলতে হবে। পরিষ্কার হতে হবে। যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল নিয়ে আলাপ হচ্ছে ও যেখানে অভিযোগ দাখিল করা হচ্ছে, সেই ট্রাইব্যুনালের ২০(২) তে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট বা ডেথ পেনাল্টি বা মৃত্যুদণ্ডের কথা উল্লেখ আছে। এই আইনের মধ্যে থাকা মৃত্যুদণ্ডের কথা আন্তর্জাতিকভাবে পুরো বিচার-প্রক্রিয়াকে তর্কের মধ্যে ফেলবে। আমাদের অনেকেরই মনে আছে, শাহবাগের আমলে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ বহু আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান সেই বিচার বা রায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। আমরা বারেবারে জাতীয়তাবাদী জোশে বলেছি, ওরা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। কিন্তু তাদের আপত্তির অন্যতম প্রধান জায়গায় ছিল ‘মৃত্যুদণ্ড’।
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মৃত্যুদণ্ডকে মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে মনে করে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিভিন্ন সময় মৃত্যুদণ্ডকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে তারা সহজ ভাষায় কিছু বক্তব্য দিয়েছে। যেমন, এটা একটি চূড়ান্ত শাস্তি, ফেরত আসার আর কোনো উপায় নেই। যেহেতু ভুল হতেই পারে আইনে, এবং দুনিয়াতে এমন বহু নজির আছে, যেখানে অনেক বছর পর নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের ফলে এই ভুল আর শোধরানোর উপায় থাকে না। পাশাপাশি, মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে অপরাধ কমেছে, পৃথিবীর কোনোখানে এমন নজির পাওয়া যায় না। সাধারণত ত্রুটিপূর্ণ বিচারব্যবস্থাতে মৃত্যুদণ্ড বেশি থাকে এবং এটাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের প্রচুর নজিরও দুনিয়াতে আছে। উল্লেখ্য, নিজামীসহ অন্যান্যদের যখন মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হয়েছিল, তখন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তাদের বিবৃতিগুলোতে বিচারপ্রক্রিয়ার ত্রুটি এবং ‘মৃত্যুদণ্ড’ নিয়ে আপত্তির কথা বারেবারে বলছিল : The crimes committed during the independence war were horrific, and there is no question that victims deserve justice. But the death penalty only perpetuates the cycle of violence.১৯
অর্থাৎ, সমগ্র দুনিয়াতে যেখানে মৃত্যুদণ্ড বন্ধের জোর প্রচেষ্টা চলছে, সেখানে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মৃত্যুদণ্ড বা ক্যাপিটাল পানিশমেন্টের উপস্থিতি এই বিচারপ্রক্রিয়াকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলবে। আইনের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধারাগুলোকে বাদ দিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।
তৃতীয়ত, অভ্যুত্থান পরবর্তী সহিংসতায় প্রচুর লোক প্রাণ হারিয়েছেন। সে সংখ্যাও শতাধিক। আজকে যখন আমরা বিচারের কথা বলছি, সেই হত্যাকাণ্ডগুলোকেও বিচারের আওতায় আনতে হবে। কেবল অভ্যুত্থানকালের হত্যাকাণ্ডকে বিচারের আওতায় আনা হলে, এবং অভ্যুত্থান পরবর্তী পর্যায়কে রেহাই দেওয়া হলে – তা হলে আমরা ইনসাফ নিশ্চিত করতে পারবো না। আবারও, সেই দুষ্টচক্রে পতিত হবো।
পুরো আওয়ামী জমানা ছিল বিচারব্যবস্থার এক দুঃসময়। গায়েবি মামলা থেকে শুরু করে ইচ্ছামাফিক রাজনৈতিক ফায়দা তোলার বাসনা থেকে রায় প্রদান পর্যন্ত - এই ছিল আওয়ামী জমানার ছিরি। আদালতের বাইরে চলছে, একের পর গুম, ক্রসফায়ার, হেফাযতে নির্যাতন ও মৃত্যুর (কাস্টোডিয়াল টর্চার ও ডেথ) ঘটনা। অর্থাৎ, বিচারপ্রক্রিয়ার এই নাজুক পরিস্থিতি মব ভায়োলেন্সের উর্বর জমিন হয়ে থাকে। আমরা যখন বলছি আমাদের ভাই হত্যার বিচার চাই, তখন অবশ্যই সেটা লামছাম কোনো বিচার আমরা চাচ্ছি না। আমরা এমন কোনো রাজনৈতিক ও ত্রুটিপূর্ণ বিচারপ্রক্রিয়া চাচ্ছি না যার মাধ্যমে জালিম আবার মজলুমে পরিণত হতে পারে। আমরা ‘ফাঁসি চাই’ বলে আর কোনো ‘ফাসিবাদ’ -এ ঢুকতে চাচ্ছি না। আমরা আসলে ইনসাফ চাই।
তথ্যসূত্রঃ
১. Henry David Thoreau, Civil Disobedience, 1849
২. Zinn, H. (1997). The Zinn reader: Writings on disobedience and democracy. Seven Stories Press.
৩. Sharp, G. (2012). From dictatorship to democracy: A conceptual framework for liberation (4th ed.). Serpent's Tail.
৪. Chenoweth, E., & Stephan, M. J. (2011). Why civil resistance works: The strategic logic of nonviolent conflict. Columbia University Press.
৫. Ammons, J. D. (2024). Institutional effects of nonviolent and violent revolutions. World Development Perspectives, 34, Article 100497.
৬. Chenoweth, E. (2023). The role of violence in nonviolent resistance. Annual Review of Political Science, 26.
৭. Beck, Colin J., and others, On Revolutions: Unruly Politics in the Contemporary World (2022; online edn, Oxford Academic, 23 June 2022), https://doi.org/10.1093/oso/9780197638354.001.0001, accessed 17 Sept. 2024.
৮. Ortiz, I., Burke, S., Berrada, M., & Saenz Cortés, H. (2021). World protests: A study of key protest issues in the 21st century. Springer International Publishing.
৯. Anam, M. (2024, July 26). Are we going to learn from our mistakes or keep repeating them? The Daily Star.
১০. দৈনিক আজাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬২.
১১. মহিউদ্দিন আহমদ, রাজনীতির মওলানা, বাতিঘর, ২০২৩.
১২. Basu, S. (2023). Intimation of revolution: Global sixties and the making of Bangladesh. Cambridge University Press.
১৩. Chakrabarty, D., Majumdar, R., & Sartori, A. (Eds.). (2007). From the colonial to the postcolonial: India and Pakistan in transition. Oxford University Press.
১৪. সারোয়ার তুষার ও সহুল আহমদ, মারণ-রাজনীতি : রাষ্ট্র ও সহিংসতার বয়ান, আদর্শ, ২০২৪.
১৫. আল-জাজিরা, ২২ আগস্ট ২০১৬.
১৬. Ahmed. S. (2024, June 18). “Genocide” vs “Self-defense”: Reflection on the ongoing extermination in Gaza. Bangla Outlook.
১৭. সুলতানা, র. (২০২৪, ২৮ আগস্ট)। সহিংসতার এপিঠ-ওপিঠ এবং বয়ান ভাঙার রাজনীতি। প্রথম আলো।
১৮. Kloppe-Santamaría, G. (2020). In the vortex of violence: Lynching, extralegal justice, and the state in post-revolutionary Mexico (1st ed.). University of California Press.
১৯. Amnesty International. (2014, October 30). Bangladesh: Death penalty will not bring justice for crimes during independence war. Amnesty International. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/10/bangladesh-death-penalty-will-not-bring-justice-crimes-during-independence-war/.
৫৩৩ তম সাপ্তাহিক লেকচার রিডিং ক্লাব ট্রাস্ট
বিষয়: জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: সহিংসতা, বয়ানের রকমফের ও ইনসাফ প্রশ্ন
বক্তা: সহুল আহমদ
সময় ও তারিখ: মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭.০০টা, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
স্থান: ৮০৩ নং রুম, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, বাংলামটর, ঢাকা