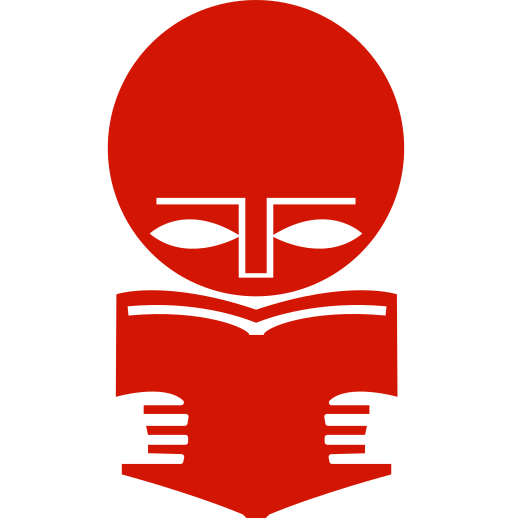
২৭৭তম সাপ্তাহিক পাবলিক লেকচার
Popular Art in Bangladesh: Special Focus on Rickshaw Paintings and Cinema Banner Paintings
বক্তা- শিল্পী শাওন আকন্দ
তারিখ- শনিবার, ২৫ আগস্ট, ২০১৭
সিনেমা ব্যানার পেইন্টিং
১৯৪৭-এর দেশভাগের পর প্রতিষ্ঠানভিত্তিক চারুকলার ধারার পাশাপাশি একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারাও গড়ে ওঠে। এর নেতৃত্ব দেন পীতলরাম সুর, আর কে দাস, আলাউদ্দিন, আলী নুর, দাউদ উস্তাদ প্রমুখ শিল্পী। এসব প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পীর মাধ্যমেই বিকশিত হয় এ দেশের সিনেমা ব্যানার পেইন্টিং, রিকশা আর্ট, ট্রাক আৰ্ট ইত্যাদি।
সিনেমার ব্যানার বলতে আমরা এখন যা বুঝি– অর্থাৎ কাপড়ের উপরে বিভিন্ন উজ্জ্বল রঙে সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রায়শই অতিরঞ্জিত প্রোট্রেট কিংবা ফিগার এবং গোটা গোটা অক্ষরে লেখা সিনেমার নাম ও অন্যান্য তথ্য— এই ধরণের কাজের সূত্রপাত দেশভাগের পর থেকেই হয়েছে।
দেশভাগের আগে ঠিক এই ধরণের সিনেমার ব্যানার পেইন্টিং-এর প্রচলন না থাকলেও, প্রচারণার তাগিদে প্রেক্ষাগৃহের নির্দিষ্ট দেয়ালে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছবি ও সিনেমার নাম বড় বড় করে লেখার প্রচলন ছিল। আমরা এই ধরণের কাজকে বলতে পারি সিনেমার ব্যানার পেইন্টিং-এর আদি রূপ। দেশভাগের আগে তিরিশ ও চলিশের দশকে, ঢাকার প্রেক্ষাগৃহের দেয়ালে এই ধরণের ছবি আঁকার কাজে যুক্ত ছিলেন এমন অন্তত একজন শিল্পীর নাম জানা যায়— তিনি শাঁখারী বাজারের পীতলরাম সুর (১৯০২-১৯৮৭)। ঢাকার ওয়াইজঘাট এলাকায় মায়া (স্টার) সিনেমার হলের কাছাকাছি অঞ্চলে তাঁর প্রতিষ্ঠান ‘আর্ট হাউজ' ছিল বলে জানা যায়। এমন কি পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকে সিনেমার ব্যানার পেইন্টিং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। উদাহরণ হিসাবে বিখ্যাত শিল্পী ও ভাস্কর নিতুন কুন্ডু (১৯৩৬-২০০৬) এবং বর্তমানে চলচ্চিত্র পরিচালক আজিজুর রহমান (জ. ১৯৩৯)-এর নাম উল্লেখ করা যায়।
দেশভাগের পর বিপুল সংখ্যক অবাঙ্গালী মুসলমান কোলকাতা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানে চলে আসে। এদের অনেকেই কোলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে সিনেমার ব্যানার পেইন্টিং কিংবা এ ধরণের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মূলত: এদের হাত দিয়েই বাংলাদেশে সিনেমার ব্যানার পেইন্টিং-এর সূত্রপাত। দেশভাগের পর কিংবা ১৯৬৪-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর কোলকাতা থেকে যারা ঢাকায় এসে কাজ শুরু করেন তাদের অনেকেই এই স্টুডিও/কারখানাগুলোতে কাজ করতো।
তবে ঢাকায় সিনেমার ব্যানার পেইন্টিং-এর ইতিহাসে আরেকজন পথিকৃৎ এর সন্ধান পাওয়া যায়, যার নাম মোহম্মদ সেলিম (পরে ‘মুনলাইট' সিনেমা হলের মালিক)। মোহম্মদ সেলিম এসেছিলেন কোলকাতা থেকে। তার আদি নিবাস ছিল বোম্বে। ১৯৪৮ থেকে তিনি ঢাকায় সিনেমার ব্যানার পেইন্টিং এর কাজ শুরু করেন তার বাসায়, র্যাংকিন স্ট্রীটে। এই সেলিমের কাছ থেকে কাজ শিখে পরবর্তী পর্যায়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন অনেকেই। এদের মধ্যে গুলফামের নাম বিশেষ উলেখযোগ্য। (গুলফাম এবং মোহম্মদ সেলিম দু'জনই মুক্তিযুদ্ধের পর পাকিস্থানে চলে যান।)
রিকশা আর্ট
নিজস্ব শিল্পশৈলী, উপস্থাপন রীতি ও বিষয়বস্তুর স্বকীয়তায় ইতিমধ্যে দেশে-বিদেশে সুধীজনের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেটি হলো রিকশা আর্ট। ব্রিটিশ মিউজিয়ামেও বাংলাদেশের সুসজ্জিত ও চিত্রিত রিকশা সংগৃহীত আছে।
মূলত চাকা আবিষ্কারের ধারাবাহিকতায় পৃথিবীতে রিকশা নামের এই বাহনের সূত্রপাত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ১৮৭০ সাল নাগাদ। অবিভক্ত বাংলায় প্রথম রিকশার প্রচলন ঘটে কলকাতায়, বিশ শতকের প্রথম ভাগে। কাছাকাছি সময়ে বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডে রিকশার প্রচলন হয় প্রথমে ময়মনসিংহ ও নারায়ণগঞ্জে এবং পরে ঢাকায় (১৯৩৮)। তবে বাংলাদেশে প্রচলন ঘটে সাইকেল রিকশার, মানুষে টানা রিকশা নয়। বাহারি ও শৌখিন পরিবহন হিসেবে ঢাকায় রিকশার আগমন ঘটে ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর। মূলত রিকশা পেইন্টিংয়ের সূত্রপাত হয় এই সময় থেকেই। পঞ্চাশ ও ষাটের দশক থেকে রিকশা পেইন্টিং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয় হতে থাকে। বাংলাদেশে রিকশা পেইন্টিংয়ের প্রবীণ ও বিখ্যাত শিল্পী যেমন- আর কে দাস, আলী নূর, দাউদ উড়াদ, আলাউদ্দিনসহ অন্যরা পঞ্চাশ ও ষাটের দশক থেকেই রিকশা পেইন্টিংয়ের সঙ্গে যুক্ত হন।
রিকশা আর্টের মূল লক্ষ্য রিকশাকে সুসজ্জিত ও আকর্ষণীয় করা। সাধারণত শিল্পীরা মহাজন এবং ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী ছবি এঁকে থাকেন। তবে গত ৫০ বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে রিকশা পেইন্টিং করা হয়েছে। যেমন- ষাটের দশকে রিকশা পেইন্টিং করা হতো মূলত শীর্ষস্থানীয় চলচ্চিত্র তারকাদের প্রতিকৃতি অবলম্বনে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধকে বিষয়বস্তু করে। আবার সত্তরের দশকে নতুন দেশের নতুন রাজধানী হিসেবে ঢাকা যখন বাড়তে শুরু করে তখন কাল্পনিক শহরের দৃশ্য আঁকা হতো রিকশায়। পাশাপাশি সব সময়ই গ্রামের জনজীবন, প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিও আঁকা হতো, এখনো হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন স্টাইলের ফুল, পাখি ইত্যাদি তো আছেই।
ট্রাক পেইন্টিং
বাংলাদেশের নগরকেন্দ্রিক চারুশিল্পের একটি চমৎকার উদাহরণ ট্রাক পেইন্টিং। মূলত অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পীদের মাধ্যমেই এ শিল্পশৈলীটি বিকাশ লাভ করেছে এবং তা এখনো বহমান। ঠিক করে ট্রাক পেইন্টিংয়ের উৎপত্তি, তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে সংশ্লিষ্ট প্রবীণ শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বাংলাদেশে এ শিল্পধারার সূত্রপাত সম্ভবত পাকিস্তান আমলে, ষাটের দশকে।
ছোট-বড় নানা ধরনের ট্রাক বিভিন্ন চিত্র দিয়ে শোভিত করার পেছনের মূল কারণটি সৌন্দর্যবর্ধন। সাধারণত আমরা রাস্তায় যে রকম ট্রাক চলতে দেখি, কেনার সময় কিন্তু এগুলো ঠিক সে রকম থাকে না। ইঞ্জিনসহ মূল কাঠামো বা চেসিসটি বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। ক্রেতা সেটি কিনে নিয়ে স্থানীয়ভাবে ট্রাকের বডি নির্মাণ করে নেন। অতঃপর গাড়ির মালিক নিজ খরচে এবং নিজের চাহিদা ও রুচিমাফিক গাড়িটি সজ্জিত ও অলংকৃত করে নেন। ট্রাক পেইন্টিংয়ের ক্ষেত্রে রংমিস্ত্রিকে বলা হয় ‘পেইন্টার'। আর্টিস্টের কাজ হলো বিভিন্ন ধরনের ছবি এঁকে ট্রাকটিকে আকর্ষণীয় করে তোলা ।
সাধারণত ট্রাকের পেছনের ডালা ('ব্যাক ডালা' নামে পরিচিত) ও সাইড বডিসহ (দুই পাশের ডালা) কেবিনের দরজায় ছবি আঁকার সুযোগ থাকে। সেই হিসেবে একটি ট্রাক বেশ বড় আকৃতির ‘ক্যানভাস'। ট্রাক পেইন্টিংয়ে শিল্পীর হাতের দক্ষতা ও কল্পনাশক্তি প্রকাশের এটি হচ্ছে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান।
সাধারণত মুসলমান মালিকের গাড়ির হুড়ে আল্লাহু বা কাবা শরিফের ছবি, মসজিদ/মাজারের ছবি খোদাই করা হয় বা আঁকা হয়। গাড়ির মালিক হিন্দু হলে বিষয়বস্তু আলাদা হতে পারে, যেমন- ওম্ চিহ্ন বা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ছবি।
বাংলাদেশের বেশ কিছু অঞ্চল ট্রাক পেইন্টিংয়ের জন্য বিখ্যাত। এর মধ্যে যশোর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, বগুড়া, ময়মনসিংহ, খুলনা, কুমিলা, ফরিদপুর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব অঞ্চলেই আছে কিছু নিজস্ব স্টাইল ও বৈশিষ্ট্য। সামনের হুডের ছবি বা প্রতীক দেখে অভিজ্ঞজনেরা বলে দিতে পারেন, এটা কোন অঞ্চলের ট্রাক বা কোন অঞ্চলের শিল্পীর আঁকা ট্রাক ।